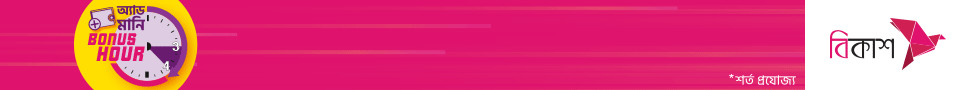বাঙালির ফুটবল উন্মাদনা
বাঙালির ফুটবল উন্মাদনার ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, এর সূচনাটা ১৩৬ বছর আগে, পরাধীন ভারতে। শুরুটা করেছিলেন নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী নামের এক বাঙালি ছাত্র, সেই ১৮৭৮ সালে। নগেন্দ্র তখন কলকাতা হেয়ার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। ক্লাসের বন্ধুদের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা চাঁদা তুলে ইংরেজদের দোকান থেকে বল কিনে যেভাবে খেলা শুরু, তাতে ফুটবলের ছিরিছাঁদ কিছুই ছিল না। ফুটবল ইতিহাসের গবেষক শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য নগেন্দ্র প্রসাদদের সেই খেলার একখানি চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে: ‘সেদিন মাঠে নামল সবাই বল নিয়ে। গোলপোস্ট-ফোস্টের বালাই নেই, এলোপাতাড়ি মার, কখনো পায়ে, কখনো হাতে বল ধরে পায়ের লাথি, আইন বা পদ্ধতির কোনো তোয়াক্কা না করেই।’ খেলার এই অদ্ভুত দৃশ্যের তামাসগিরও কম হলো না। মাঠের উত্তর দিক থেকে এল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা আর পূর্ব দিক থেকে হিন্দু স্কুলের ছেলেরা। পথ-চলা কিছু লোকও দাঁড়িয়ে গেল এই কিম্ভূতকিমাকার খেলা দেখতে।
কত দিন এভাবে চলেছিল, ঠিক জানা যায় না। হয়তো কয়েক দিন মাত্র। প্রেসিডেন্সির ছাত্ররাই এল তাদের অধ্যাপক বি.ভি স্ট্যাককে নিয়ে। খেলা দেখে তো তিনি হেসেই মরেন। ভাবেন, এ কোন ফুটবল? খেলোয়াড়দের বললেন, তোমরা যা নিয়ে খেলছ, সেটি রাগবি বল। আর যা খেলছ, তা না রাগবি, না ফুটবল। আমি কাল একটা ফুটবল নিয়ে আসব আর আইনকানুনও তোমাদের শিখিয়ে দেব। পরদিন কথামতো এলেন সেই সাহেব একখানা চমৎকার বল নিয়ে। ছাত্রদের দুই ভাগে ভাগ করে খেলার আইনকানুন বলে দিলেন। তারপর মুখে বাঁশি নিয়ে নেমে গেলেন রেফারির ভূমিকায়। এভাবেই শুরু বাংলার ফুটবলের ইতিহাস। এর উদ্ভাবক নগেন্দ্র প্রসাদ আর আঁতুড়ঘরে ধাত্রী স্ট্যাক সাহেব। সেই থেকে শুরু বাংলার ফুটবল।
১৮৭৮ থেকে ১৮৯৪—এই ষোলো বছরে বাংলার ফুটবল কৈশোর-উত্তীর্ণ এক টগবগে তরুণে পরিণত হলো। নগেন্দ্র প্রসাদ ১৮৮৪ সালে কলকাতায় ওয়েলিংটন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলেন। এক বছর পরে এর পরিবর্তিত নাম হলো টাউন ক্লাব। ১৮৮৫ সালেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো শোভাবাজার ক্লাব। এর স্রষ্টাও ওই নগেন্দ্র প্রসাদ। বছর তিনেকের মধ্যে বেহুদা লাথালাথিটাকে একটা ছন্দের মধ্যে এনে ১৮৮৯-এ শোভাবাজার ক্লাব ব্রিটিশ ভারতীয় উন্মুক্ত ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কিন্তু শোভাবাজারের তিন বছর চেষ্টাও যথেষ্ট পোক্ত না হওয়ায় প্রথম খেলাতেই তিন গোলে হেরে বিদায়। নগেন্দ্র প্রসাদ তবু হাল ছাড়েননি। ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো আইএফএ বা তৎকালীন ভারতবর্ষের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সেখানেও আছেন নগেন্দ্র প্রসাদ। ১৮৯৫ থেকেই যাত্রা শুরু হলো কেতা মাফিক উপমহাদেশের ফুটবলের। আর বাঙালিরাই এই আধুনিক ফুটবলের পথিকৃৎ।
প্রথম দিকে নিজেদের মধ্যেই খেলা হতো। পরে শক্তি সঞ্চয় করে শাসক ব্রিটিশদের নানা স্থানীয় দলের সঙ্গে পাল্লা শুরু। তখন ভেতরে ফুটবল চেতনার সঙ্গে ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার একটা গোপন ইচ্ছাও জেগে উঠছিল। তাই লালমুখো গায়ে-গতরে লম্বা-চওড়া, দঁুদে ইংরেজদের সঙ্গে বেটেখাটো কালো-কোলো নাঙ্গা পায়ের ভারতীয়দের খেলা অনেকটা যেন গোরা-কালার যুদ্ধে রূপ নিতে থাকে। ওপরে খেলা, ভেতরে ভেতরে যেন একটা যুদ্ধজয়ের ইচ্ছা। রাজনৈতিক চেতনার এই ছাপে খেলাটা নতুন মাত্রা পেল। দাঁতে দাঁত কামড়ে খেলতে শিখল বাঙালি ছেলেরা। শারীরিক শক্তি কম, পায়ে বুট নেই, তাতে কী? বল নিয়ে ছলাকলায় পারদর্শিতা এল বাঙালিদের।
১৮৭৮ সালে ভারতীয় ফুটবলের যে যাত্রা শুরু, তার ঠিক ৪১ বছরের মাথায় ইংরেজদের দুর্গ চুরমার করে বাঙালি শিবদাস ভাদুরীর নেতৃত্বে কলকাতা মোহনবাগানের ঘরে উঠল আইএফএ শিল্ড। মোহনবাগান ক্লাবের ১১ জন খেলোয়াড়ই ছিলেন বাঙালি এবং বাংলাদেশের দারুণ গৌরবের ব্যাপার এই যে ১১ জনের ১০ জনই জন্মসূত্রে পূর্ববাংলার বাঙাল।
পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের ফুটবল ঐতিহ্যও কিন্তু গর্ব করার মতোই। যত দূর জানা যায়, ঢাকা কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮৪১) পূর্ববাংলার ফুটবলের সূতিকাগার। এই কলেজের এক ইংরেজ অধ্যাপক উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁর ছাত্রদের ফুটবল খেলায় টেনে আনেন। ঢাকা ও মফস্বলে গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি ফুটবল ক্লাব। এর মধ্যে ঢাকার ওয়েলিংটন ক্লাব খুব পুরোনো। প্রকৌশলী রামদাস ভাদুরী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। এই পরিবারেরই সদস্য শিবদাস ভাদুরী ও বিজয়দাস ভাদুরীও তুখোড় খেলোয়াড়। ওয়েলিংটন ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রাখা হয় ওয়ারী ক্লাব । ১৯১০-এ ঐতিহ্যবাহী ওয়ারী ক্লাব কুচবিহারের রাজার শক্তিশালী দলকে পরাজিত করে। আর ওই বছরই ক্লাবটি আইএফএ খেলার অনুমোদন পায়। ঢাকার ফুটবল ইতিহাসে সেকালের ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশন বা ডিএসএ-র অবদান বিরাট।
ইংল্যান্ডের একটি বিখ্যাত ফুটবল দল আইলিংটন কোরিন্থিয়ান দেশের বাইরে গিয়ে ফুটবলকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস চালায়। তাদের বলা হতো ব্রিটেন ও ফুটবলের রাষ্ট্রদূত। এরাই ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ফুটবল নিয়ে যায়। ফুটবলকে দেয় আন্তর্জাতিক রূপ। এদের প্রভাবেই ব্রাজিল দলটি ধীরে ধীরে বিশ্ব ফুটবলে একটি পরাশক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে।
কোরিন্থিয়ান ছিল শক্তিশালী পেশাদার দল। ঢাকায় তাদের খেলা ২১ নভেম্বর, ১৯৩৭-এ ডিএসএ দলের সঙ্গে। সেই ঐতিহাসিক খেলার একটি বর্ণনা তুলে ধরছি: ‘মন্টু ঘোষ বল নিয়ে দৌড়ুচ্ছেন। কোরিন্থিয়ানরাও ছুটছেন মন্টু ঘোষের পেছনে। মন্টু হঠাৎ বল ঠেলে দিলেন পেছনে দাঁড়ানো পাখি সেনকে (আসল নাম বি. সেন)। বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড় ছিলেন না তাঁর কাছে। গোলকিপারও বলের গতি আঁচ করতে পারেননি। পাখি সেন মওকা মতো বল পেয়ে বল ঢুকিয়ে দিয়েছেন গোলে। ঢাকার মাঠের কয়েক হাজার দর্শকের সে কী উল্লাস! যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।’ (দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ, পৃষ্ঠা ২৬)। সেই অলৌকিক গোলের ইতিহাস নির্মাতা পাখি সেন তখন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। খেলার অধিনায়ক ছিলেন এস মিত্র। কোরিন্থিয়ান দলটি বার্মা ও দূরপ্রাচ্যে কোনো খেলায় হারেনি। কলকাতায়ও জিতেছে, শুধু ড্র করেছে কলকাতা মোহামেডানের সঙ্গে। কিন্তু ঢাকায় এসে হেরে গেল ১-০ গোলে। সে জন্যই কোরিন্থিয়ানের অধিনায়ক পি বি ক্লার্ক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন: ‘বাংলার রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম শুনেছিলাম। এবার চোখে দেখলাম।’ (ওই, পৃষ্ঠা ২৬)।
বাংলার ফুটবল গৌরবের জাদুকর সামাদের নামটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বলা হয়, বল তাঁর পায়ে আঠার মতো লেখে থাকত। বল নিয়ে তিনি যা খুশি তাই করতে পারতেন। কৌশলে, চাতুর্যে, ভোজবাজিতে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে তাঁর পা-শরীর-মাথা ও বল যেসব পরিস্থিতি ও দৃশ্যের অবতারণা করত, বিপক্ষ দলের কাছে তা ছিল অভাবনীয়। বল নিয়ে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাণ্ড করার জন্যই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ফুটবলের প্রবাদপুরুষ, অতুলনীয় জাদুকর। খুব মজা পেতেন বলে লাথি না দিয়ে গোল করতে। গোলকিপারকে যেন সম্মোহিত করে বল নিয়ে ঢুকে যেতেন গোলপোস্টের ভেতরে। কখনো কখনো সব খেলোয়াড়কে কাটিয়ে নিয়ে গোলকিপারকে একা পেয়েও করুণা করে গোল না দিয়ে বল নিয়ে ফিরে আসতেন মাঠের একপ্রান্তে। শুরু করতেন গ্যালারি শো। দর্শক মাতানোর তাঁর এই কৌশল তাঁকে কিংবদন্তিতে পরিণত করে।
২.
১৯৫০-এর দশকে ঢাকা স্টেডিয়াম নির্মিত হওয়ার পরে ফুটবল খেলা বেশ জমাটি হয়ে ওঠে। মোহামেডান, ওয়ান্ডারার্স, ওয়ারী ক্লাব, আজাদ স্পোর্টিং বেশ জনপ্রিয় দল তখন। মোডামেডান ও ওয়ান্ডারার্সের মধ্যে সে সময় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতো। দর্শকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই দলকে সমর্থন করত। আজাদ স্পোর্টিং ছিল ছিমছাম ও নান্দনিক ফুটবলের দল। ছন্দময় ফুটবল অনুরাগীদের অনেকেই ছিলেন এই দলের সমর্থক। এই চারটি দলকে নিয়েও ফুটবল উন্মাদনা কম ছিল না। কৈশোরত্তীর্ণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একসময় ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ফুটবলার ছিলেন।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শেখ কামাল প্রতিষ্ঠা করেন আবাহনী ক্রীড়াচক্র । এই দলের নান্দনিক কৌশলময় খেলা বিপুল দর্শকের চিত্তজয় ও উন্মাদনায় বিশাল ভূমিকা রাখে। মোহামেডান আর আবাহনীর খেলার দিনটি তখন হয়ে উঠত দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ। ঢাকার মাঠে আবাহনী এবং কলকাতা মোহামেডানের একটি অবিস্মরণীয় গোলের কথা বলেই এই অধ্যায় শেষ করি। আবাহনীর স্ট্রাইকার কাজী সালাউদ্দীন রাইট আউট পজিশনের এক জটিল কোণ থেকে এক অবিস্মরণীয় কিকে কলকাতা মোহামেডানের অসাধারণ গোলরক্ষক রহমতউল্লাহকে যেভাবে ফাঁকি দিয়ে গোল করেছিলেন, সেটি কখনো ভোলার নয়।
বিশ শতকের শুরু থেকেই পূর্ববাংলার গ্রামেগঞ্জে ফুটবল বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই ধারাবাহিকতায় টেলিভিশনের যুগে বাংলাদেশে এল বিশ্ব ফুটবলের এক মনমাতানো উপহার। বিশ্বকাপ এলে বোঝা যায় বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের কী উন্মাদনা! বাংলাদেশ দল খেলছে না। তাতে কী? বাঙালির রক্তে আছে ফুটবলের নেশা। অতএব সমর্থন করো নান্দনিক ফুটবলের কারিগর ব্রাজিল, না হয় আর্জেন্টিনাকে। এ দুই দলের ভক্তে বিভক্ত সারা বাংলাদেশের ফুটবল-পাগল দর্শক। কিছু কিছু সমর্থক জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স বা আফ্রিকার কোনো কোনো দলের। শুধু কি সমর্থন, বিভিন্ন দেশের পতাকায় পতাকায় ছেয়ে যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ফুটবলপ্রিয় মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, উঁচু গাছ, বা দালানকোঠার শীর্ষ। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় আমিনবাজারসংলগ্ন নানা প্রত্যন্ত এলাকায় বা হেমায়েতপুর-সিংগাইর রোডের দুদিকের ঘরবাড়িতে। কোনো কোনো দর্শক চমক দেওয়ার জন্য সর্ববৃহৎ পতাকা উড়িয়েও বাজিমাত করতে চায়। তিরিশ বা চল্লিশ ফুট বা আরও লম্বা পতাকাও তৈরির গোপন প্রতিযোগিতা চলে।
বিশ্বকাপ উপলক্ষে এই ফুটবল উন্মাদনাকে একটি ইতিবাচক ঘটনা বলেই আমরা মনে করি। বিশ্বকাপের অন্তত একটা মাসজুড়ে এই নান্দনিক ফুটবল উপভোগের উন্মাদনায় মানুষ, বিশেষ করে তরুণেরা মারদাঙ্গা, চাঁদাবাজি, হিংসা-জিঘাংসা, খুন-জখম বা হিংস্র আচরণ বাদ দিয়ে যে মেতে থাকে, তাতে সামাজিক সংহতি এবং শুভচেতনা দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করে। সূত্রঃ প্রথম আলো